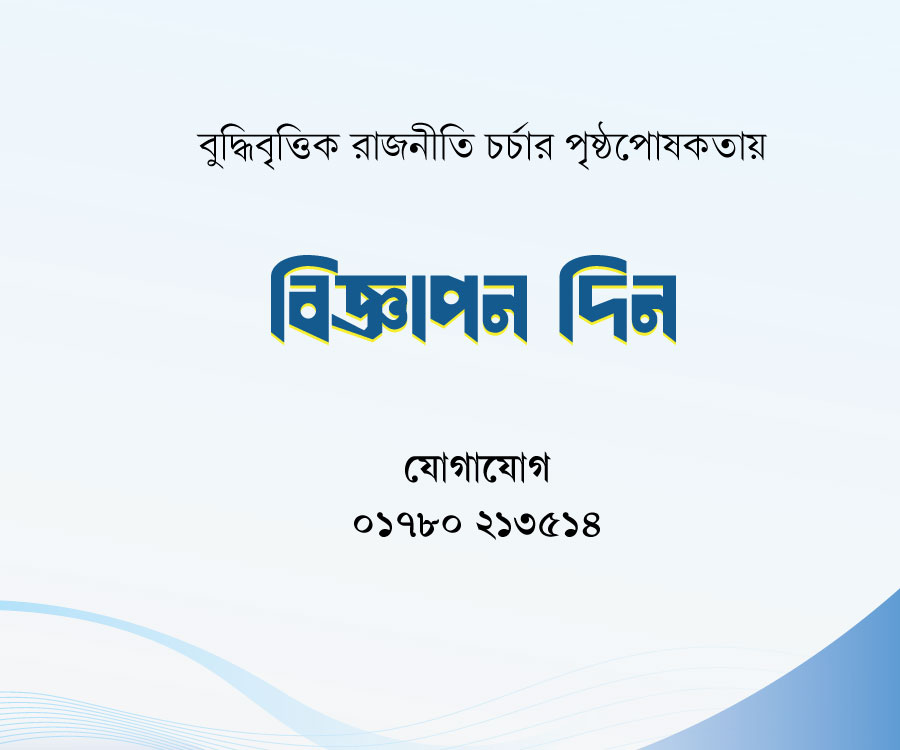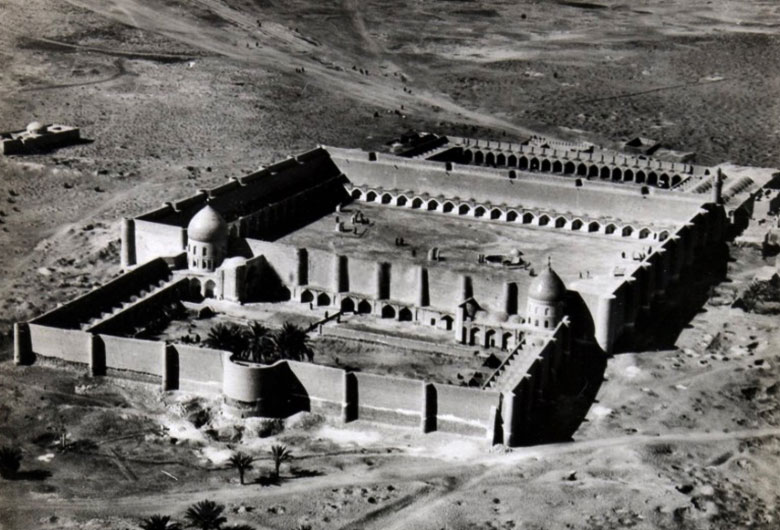ডিসেম্বর/২০২৪/মতামত ও পর্যালোচনা/চলতি প্রসঙ্গ
ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে কি এখন ভাবা যায়?
পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের আকাশ সমান আকাঙ্ক্ষার অতি সামান্যই পূরণ করতে পেরেছেন প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অভ্যন্তরীণ সরকার। এক রক্তাক্ত প্রতিরোধ ও ‘গণবিস্ফোরণ’র মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধানসহ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব নেতা পালিয়ে গেলেও সে সময় রাজনৈতিকভাবে অনভিজ্ঞ ছাত্র-জনতা ব্যর্থ হয়েছিলো ‘বিপ্লবী সরকার’ গঠনে। যদিও এটা তাদের দোষ নয়, বিগত ১৫ বছরে ‘আওয়ামী লীগ’ সরকারের পতন ছাড়া অন্য কোনো গঠনমূলক রাজনীতি করার কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে তারা কখনো ভাবেনি, স্বৈরাচারের পতন পরবর্তী সময়ে কী হতে পারে পরিস্থিতি! সে শুন্যতায় বিপ্লবী সরকারের পরিবর্তে ফ্যাসিবাদী সরকারের রাষ্ট্রপতির অধীনেই তাদের সরকার গঠন করতে হয়। যদিও অব্যবহিত পরে এই সাংবিধানিক সরকারের দায় বিএনপির উপর আরোপ করেছিলো। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে সেটা হওয়ারই কথা ছিল, কেননা ভোটের রাজনীতি কিংবা একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বিবেচনা করলে সংবিধান সমুন্নত রাখার এই পদক্ষেপ বিএনপি’র জন্য লাভজনক। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে যে তারা-ই একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি সে অবস্থান থেকে ৫ আগস্টের স্টেকহোল্ডারদের সাংবিধানিক সরকার গঠনে রাজি করাতে পারাটা ছিল বিএনপিরই একচেটিয়া সফলতা।
এর ফলে যা ঘটলো তা হলো- দেশে
একটা না সাংবিধানিক, না বৈপ্লবিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। তাদের অবস্থান বৈপ্লবিক, কিন্তু হাত-পা বাঁধা থাকলো আওয়ামী লীগ সরকারের প্রণীত দমন-পীড়ন
ও অনৈতিক আইন-কানুন দ্বারা। শুরুতেই ভারতে ইলিশ রপ্তানি বিষয়ে সরকারের অবস্থান ও রপ্তানিতে
বাধ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই সময়ে তারা ব্যর্থ হয়েছিলো রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের
অন্তর্ভূক্তিতে। অভ্যন্তরীণ সরকারে এনজিও-কেন্দ্রিক সমাজসেবকের পাশাপাশি প্রয়োজন ছিল
বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ। কিন্তু তা হলো না। এই ব্যর্থতার জেরে এখনো জাতীয়
ও আন্তর্জাতিক বহু রাজনৈতিক প্রশ্নে সরকারকে হোঁচট খেতে হচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে
আওয়ামী লীগের প্রত্যাবর্তন যদি না হয়, তার কারণ হবে বিএনপির রাজনৈতিক কৌশল। যে প্রশ্নে
অভ্যন্তরীণ সরকার গুরুত্বহীন।
কিন্তু যে জাতীয় প্রশ্নের বাইরে
অথচ রাষ্ট্রেরই বৃহৎ স্বার্থে ছাত্র-সমাজের অবদান রাখার আছে, এমনকি জরুরিও বটে তা হলো
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন। দীর্ঘ ৩ দশক ধরে এই সেক্টরে আমাদের
ব্যর্থতা ভয়াবহ। এর জন্য দায়ী যেমন ক্ষমতাসীনদের ক্যাম্পাসের ক্ষমতা হারানোর ভয়, তেমনি
ছিল প্রশাসনের চাটুকারি আচরণ। সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রশাসনগুলো বারবার শিক্ষার্থীদের
এই রাজনৈতিক অধিকার হরণ করেছে। অথচ বাহান্ন’র ভাষা আন্দোলন, বাষট্টি’র শিক্ষা আন্দোলন,
ছেষট্টি’র ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যূত্থান, একাত্তর’র মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচার
বিরোধী কিংবা চব্বিশের জুলাই বিপ্লব সবকিছু বাস্তবায়নের মূল কারিগর ছিল এই ছাত্র সংসদগুলো।
নেতৃত্বে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক নেতা-কর্মীরা।
সর্বশেষ ২০১৯ সালে যখন ২৮ বছর
পর ডাকসু নির্বাচন হয়েছিলো। তখন আমি সাংবাদিকতায় সক্রিয়। সে সময় ‘আশার আলো’ না দেখলেও
ভাবা হয়েছিলো যে ডাকসু নির্বাচন হয়তো জাদুঘর থেকে ফিরেছে। কিন্তু দলীয় রাজনীতির ঘৃণ্য
প্রদর্শনসহ তৎকালীন দলকানা প্রশাসন একটি ‘আই-ওয়াশ’ নির্বাচন দিয়েছিলো। চরম বিক্ষোভের
হাত থেকে বাঁচতে সে সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ছাত্রনেতা নূরুল হক নূরকে ভিপি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভর্তি-পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে অনশন করা শিক্ষার্থী-সমাজকর্মী আখতার হোসেনকে
সমাজসেবা সম্পাদক করে বাকি পদগুলো ছাত্রলীগ সমর্থিত প্রার্থীদের বন্টন করে দেয়। ভোট
গ্রহণে দুর্নীতির অভিযোগতো ছিলই। সন্তুষ্ট ছিল না কোনো পর্যবেক্ষকই। দেশের শীর্ষ শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনকে নিষ্কলঙ্ক করতে নূন্যতম চেষ্টা করেনি প্রশাসন।
ইতিমধ্যে ডাকসুর ৫ বছর পেরিয়েছে।
জাকসু নির্বাচন হয়নি ৩২ বছর, চাকসুও ৩৪ বছর, রাকসু নির্বাচন হয়নি ২৯ বছর। মূলত যে সময়
একযোগে ডাকসু, রাকসু, চাকসু ও জাকসু নির্বাচন হয়েছিলো, সে সময় ক্ষমতায় স্বৈরাচার এরশাদ
সরকার। ঠিক কি কারণে জানা নেই তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারগুলো বছরের পর বছর শিক্ষার্থীদের
এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গেছে। তারুণ্যে নেতৃত্বে তৈরি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো
উন্নয়নে সরব ভূমিকা রাখা এ নির্বাচন প্রক্রিয়ার এই স্থবিরতা যে জাতীয় রাজনীতির স্থবিরতার
চেয়ে ভয়ঙ্কর তা-ই নয়। বরং জাতীয় রাজনীতির এই বেহাল দশার জন্য দায়ীও এই ছাত্র-সংসদ নির্বাচনের
স্থবিরতা। দীর্ঘ তিন দশক এদেশের শিক্ষার্থীরা দলীয় রাজনীতির বাইরে কিছু ভাবার সুযোগই
পায়নি, তার পরিণতিই এই দেড় দশকের স্বৈরাচারী শোষণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘রাজনীতি’ বলতে ছাত্রসমাজের
সামনে দিনের পর দিন শ্রেফ একটা দানবীয় হেলমেট বাহিনীর নমুনাই দেখাতে পেরেছে প্রশাসন।
যেখানে রাজনীতিসম্পৃক্ত ব্যক্তিরা শুধু গুম-খুন ও নৃশংস হামলার সঙ্গেই জড়িত। ছাত্রলীগ
ব্যতিত অন্য রাজনৈতিক তৎপরতা চললেও তাতে নূন্যতম সহযোগিতা ছিল না ধ্বজাধারী প্রশাসনের।
যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যখন জাতীয় রাজনীতির অংশ হতে গিয়েছে তাদের কাছে
অবশিষ্ট ছিল দলীয় রাজনীতির এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, ছিল না দেশ ও দেশের মানুষের জন্য করার
মতো মানসিকতা।
আজকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খামখেয়ালিপনা,
প্রশাসনের জবাবদিহিতার অভাব- মোটকথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অকার্যকর হওয়ার পিছনে ছাত্র-সংসদ
নির্বাচন না হওয়া। শিক্ষার্থীদের দলীয় রাজনীতির বাইরে ফর্ম করতে না দেওয়া। ফলে আমরা
পায়নি রুহুল কবীর রিজভী, মাহমুদুর রহমান মান্না কিংবা আমানউল্লাহ আমানদের উত্তরাধিকার।
রাষ্ট্র সংস্কারের মধ্যে যেমন
শিক্ষার সংস্কার জরুরি তেমনি দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে জরুরি ছাত্র-সংসদ নির্বাচনের
সংস্কার ও নিয়মিত আয়োজন। বর্তমান প্রশাসন ছাত্রদের নিয়োগকৃত বলা যায় (যদিও তাঁদের নিয়োগের
এখতিয়ার তাদের নেই, তবে সমর্থিত অবশ্যই) সুতরাং এই পরিস্থিতিতে ছাত্র-সংসদ নির্বাচন
প্রক্রিয়ার সংস্কার এনে তা অায়োজনে প্রশাসনে বাধ্য করার আইন করা জরুরি।
এমনকি পরিবর্তিত এই রাজনৈতিক
পরিস্থিতিতে জাতীয় নির্বাচনের আগে সুষ্ঠু ও কাঠামোগত প্রক্রিয়ায় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
আয়োজনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন
আনা েযতে পারে। বর্তমানে যে প্রজন্ম বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজনীতি বুঝতে পারে বলে
ধরা হয়, তাদের মাধ্যমে যদি এই যাত্রা আরম্ভ না হয় তবে পুনরায় তা দীর্ঘমেয়াদি টানাপোড়েনের
সম্মুখীন হবে। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ সরকারের আমলে ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতার বন্টন
কি শুধু ‘প্যারাডাইম শিফট্’ করে কিনা, নাকি নতুন ধারার রাজনীতির হাতছানি দেয় তাও দেখার
বিষয়। অন্যদিকে এই জন্য এটি এই সরকারের আমলে করতে হবে কারণ রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ
করার পর তাদের স্বার্থে এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে অবস্থান করতে পারে, যা স্বাভাবিক। কেউই
চাইবে না, রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকে ক্যাম্পাসে নিজেদের ক্ষমতা হারাতে।
একই সঙ্গে বর্তমান সময়ের ছাত্র-উপদেষ্টাদের
নির্বাচন দেওয়ার যে আগ্রহ তা দেখে আশান্বিত হওয়াও কঠিন। ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতি
বা ক্ষমতা তাদের অধীনে; ‘সমন্বয়ক’ ব্যানারে প্রশাসন থেকে হলের বিছানা পর্যন্ত তারা
দখল নিতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তারা আত্মবিশ্বাসী যে ফলাফল তাদের পক্ষেই যাবে। অর্থাৎ নির্বাচন
প্রক্রিয়ায় সংস্কার না এনে নির্বাচনে যদি ক্ষমতাসীনদের কেউ আগ্রহীও হয়ে থাকে সে দিকে
আমাদের নজর দেওয়াটাও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।
অন্যদিকে ডাকসু নির্বাচন ও
গঠনতন্ত্র নিয়ে সরব হয়েছে বেশকিছু বিকল্পধারার সংগঠন। েযখানে ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর
ছাত্র-শাখার কোনো অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তারা হয়তো সংশোধন চায়ও না। ছাত্র-সংসদের
গঠনতন্ত্রের সংস্কার তাদের ক্ষমতাকে সংকুচিত করবে বলে তাদের ধারণা কেননা। রাষ্ট্রক্ষমতায়
যদি তাদের দল থাকে তবে সহজেই ক্যাম্পাসে তারা দখলদার হয়ে উঠবে, সেখানে শিক্ষার্থী-বান্ধব
সংস্কার তাদের মাথা ব্যথারও কারণ। কিন্তু জাতীয় স্বার্থে এই সংস্কারে সবার অংশগ্রহণ
জরুরি। জরুরি গণ আলোচনাও।
এই অভ্যন্তরীণ সরকারের আমলে
আমরা আশা করতেই পারি। শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ
নিয়মিত ছাত্র-সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর এই প্রক্রিয়া শুধু ডাকসু নয়, রাকসু, জাকসু
ও চকসুসহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদগুলোর কথাও ভাবতে হবে। কেননা বারবার
প্রমানিত হয়েছে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার
কাল থেকে আজ পর্যন্ত ছাত্ররাই সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে।
মুসফিকুর রহমান
মুসফিকুর রহমান তরুণ িচন্তক ও অ্যাকাডেমিশিয়ান। বর্তমানে ডায়াস্পোরা সাহিত্য নিয়ে পিএইচডি গবেষণা করছেন ভারতে। বুদ্ধিবৃত্তিক সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এক সময়। বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয়তাবাদী ওয়েবম্যাগ ‘আন্তঃএশিয়া’র চিফ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ‘তুলনামূলক সাহিত্যের তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ’ (অসমীয়া ভাষা থেকে অনুদিত)
আরো পড়ুন